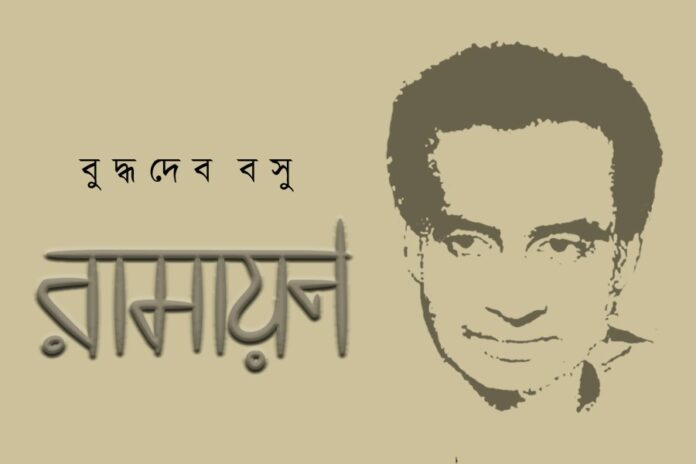বুদ্ধদেব বসু
(বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বুদ্ধদেব বসু রামের চরিত্র ও রামায়ণ সম্পর্কে তাঁর এই বিশ্লেষণকে তুলে ধরেছিলেন ১৯৪৭ সালে। বানান অপরিবর্তিত রেখে নতুন করে লেখাটি প্রকাশ করা হল।)
ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জীবনে প্রথম যে বইতে আমি জেনেছিলুম, সেটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘ছোট্টরামায়ণ’, ছোট্ট, সচিত্র, বিচিত্র, বিচিত্র-মধুর, সে-বই ছিলো আমার প্রিয়তম সঙ্গী। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পদলালিত্যের আদর খেতুম, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের ‘শিশু’ পত্রিকার পাতাবাহারে চোখ জুড়োতো— কিন্তু এমন নেশা ধরতো না আর-কিছুতেই। বার-বার পড়তে-পড়তে সমস্ত বইখানা আমার রসনাগ্রে অবতীর্ণ হয়েছিলো, -কিন্তু শুধু পদাবলি আউড়েই আমার তৃপ্তি নেই, রাম-লীলার অভিনয়ও করা চাই। বাঁশের তীরধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনের রঙ্গমঞ্চে আমার লম্ফঝম্ফ: আমিই রাম এবং আমিই লক্ষ্মণ, আর ওই যে মাচার লাউ- কুমড়ো ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরে সেজে আছে— ঐ হ’লো তাড়কা রাক্ষসী। সীতাকে না-হ’লেও তখন আমার চলতো, এমনকি, রাবণকে না-হ’লেও— কেন না রাম- লক্ষ্মণের বনবাসের অমন অপরূপ ফুতিটা মাটি হ’লো তো সীতা-রাবণের জন্যই। কী ভালো আমার লাগতো সে-সব নদী, বন, পাহাড়— পম্পা, পঞ্চবটী, চিত্রকূট— ছবির মতো এক-একটি নাম— ছবির মতো, গানের মতো, মন্ত্রের সম্মোহনের মতো উপেন্দ্রকিশোরের মুখবন্ধ :
বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে,
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে।
খড়ের কুটিরখানি গাছের ছায়ায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বড়ো সুন্দর কথা, শোনো মন দিয়া।
‘চঞ্চল’-এর যুক্তবর্ণ নিয়ে আমার রসনা সুখাদ্যের মতো খেলা করতো, তার অনুপ্রাসের অনুরণনে বুক কাঁপতো আমার। যোগীন্দ্র সরকার পদ্য পড়িয়েছিলেন অনেক, কিন্তু কবিতার জাদুবিদ্যার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।
কৃত্তিবাসের সঙ্গে পরিচয় হ’লো আরো একটু বড়ো হ’য়ে। কৃত্তিবাস আমাকে কাঁদালেন, বোধহয় দুই অর্থেই— কেন না যদিও মনে পড়ে সীতার দুঃখে চোখে জল এসেছে, তবু সে-রকম অসম্ভব ভালো লাগার কোনো স্মৃতি মনে আনতে পারি না। বয়স যখন কৈশোরের কাছাকাছি তখন একখানা মূল বাল্মীকি উপহার পেয়েছিলুম— তার পাতা ওল্টাবার মতো উৎসাহ যখন আমার হ’তে পারতো তার আগেই বইখানা হারিয়ে গেলো। আর তারপর এই এত বছর কাটলো। এর মধ্যে অনেকবার মনে হয়েছে বাল্মীকি প’ড়ে দেখবো— অন্তত চেখে দেখবো— কিন্তু এই অপব্যয়িত জীবনের অনেক সাধু সংকল্পের মতো এটিও বিলীন হ’য়ে গেছে ইচ্ছার মায়ালোকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের কল্যাণে মূল মহাভারতের স্বাদে আমার মতো অবিদ্বানও বঞ্চিত নয়, কিন্তু বাল্মীকি আর বাঙালির মধ্যে দেবভাষার ব্যবধান উনিশ-শতকী উদ্দীপনার দিনে কেন ঘোচানো হয় নি জানি না। হয়তো কৃত্তিবাসের অত্যধিক লোকপ্রিয়তাই তার কারণ। বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক নন, তিনি রামায়ণের বাংলা রূপকার; তাঁর কাব্যে রাম লক্ষ্মণ সীতা শুধু নন, দেব দানব রাক্ষসেরা সুদ্ধু মধ্যযুগীয় গৃহস্থ বাঙালী চরিত্রে পরিণত হয়েছেন, গ্রন্থটির প্রাকৃতিক এবং মানসিক আবহাওয়া একান্তই বাংলার। এ-কাব্য বাঙালীর মনের মতো হ’তে পারে, এমনকি বাংলা সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্মের প্রথম উদাহরণ ব’লেও গণ্য হ’তে পারে, কিন্তু এর আত্মার সঙ্গে বাল্মীকির আত্মার প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের ‘কচ ও দেবযানী’র সঙ্গে মহাভারতের দেবযানী-উপাখ্যানের প্রভেদের মতোই, মাপে ঠিক ততটা না-হ’লেও জাতে তা-ই। আমাদের আধুনিক কবি-ঠাকুরদের প্রশংসায় আমরা কখনো ক্লান্ত হবো না, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখবো যে আদিকবিদের চরিত্রলক্ষণ জানতে হ’লে আদিকবিদেরই শরণাগত হ’তে হবে। ভুল করবো, মারাত্মক ভুল, যদি মনে করি কৃত্তিবাসের রম্য কাননে আদিকবির, মহাকাব্যের, ধ্রুপদী সাহিত্যের, ফল কুড়োনো সম্ভব। বাল্মীকিতে রামের বনবাসের খবর পেয়ে লক্ষ্মণ খাঁটি গোঁয়ারের মতো বলছেন, ‘ওই কৈকেয়ী-ভজা বুড়ো বাপকে আমি বধ করবো’; বনবাসের উদ্যোগের সময় রাম সীতাকে বলছেন, ‘ভরতের সামনে আমার প্রশংসা কোরো না, কেন না ঋদ্ধিশালী পুরুষ অন্যের প্রশংসা সইতে পারে না’; এবং লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধের পরে সীতাকে যখন রাম পরিত্যাগ করলেন, তখন সীতা তাঁকে বললেন প্রাকৃতজন, অর্থাৎ ছোটোলোক— এই সমস্তই, সতীত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও পুত্রত্বের আদর্শরক্ষার খাতিরে বর্জন করেছেন ব’লে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কৃত্তিবাসকে তারিফ করেছেন। হয়তো তারিফ করাটা ঠিকই হয়েছে, হয়তো এর ঐতিহাসিক কারণ ছিলো, তৎকালীন বঙ্গসমাজের পটভূমিকায় এর সমর্থনও হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব— কিন্তু সে-সব যা-ই হোক, এই বর্জনে আদিকবির আত্মা যে উবে গেলো তাতে সন্দেহ নেই। আদিকবির লক্ষণ, পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য আমি যা বুঝেছি, তার নাম দিতে পারি বাস্তবতা, সে-বাস্তবতা এমন সম্পূর্ণ, নিরাসক্ত ও নির্মম যে তার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রিয়ালিজম-এর চরম নমুনাও মনে হয় দয়ার্দ্র। যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ সত্য, মহাকাব্য তারই নির্বিকার দর্পণ; মহাকাব্যে ট্র্যাজেডির মত্ততা নেই, কমেডির উচ্ছলতা নেই; তাতে গলা কখনো কাঁপে না, গলা কখনো চড়ে না; বড়ো ঘটনা আর ছোটো ঘটনায় ভেদ নেই— সমস্তই সমান, আগাগোড়াই সমতল— এবং সমস্তই ঈষৎ ক্লান্তিকর। বস্তুত, মহাকাব্য তো পৃথিবীর সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি, যখন পর্যন্ত সাহিত্য একটি সচেতন শিল্পকর্মরূপে মানুষের মনে প্রতিভাত হয় নি; এবং পরবর্তীকালে সাহিত্যকলার বিচিত্র ঐশ্বর্য যুগ-যুগ ধ’রে অবিরাম উদ্ভাসিত হ’তে পারতো না, যদি আদিকাব্যের সেই কৈশোর- সরলভাবকে, সেই অচেতন সত্যনিষ্ঠাকে মানুষ চিরকালের মতো পরিত্যাগ না-করতো। মহাকাব্যের বাস্তবতা এমনই নির্ভীক যে সংগতিরক্ষার দায় পর্যন্ত তার নেই; তুচ্ছ আর প্রধানকে সে পাশাপাশি বসায়, কিছু লুকোয় না, কিছু ঘুরিয়ে বলে না, বড়ো বড়ো ব্যাপার দু-তিন কথায় সারে, এবং সবচেয়ে বড়ো ব্যাপারে কিছুই হয়তো বলে না। মানবস্বভাবের কোনো মন্দেই তার চোখের পাতা যেমন পড়ে না, তেমনি ভালোর অসম্ভব আদর্শকেও নিতান্ত সহজে সে চালিয়ে দেয়। সেইজন্য মহাভারতে দেখতে পাই চিরকালের সমস্ত মানবজীবনের প্রতিবিম্বন: তাতে এমন মন্দেরও সন্ধান পাই যাতে এই ঘোর কলিতে আমরা আঁৎকে উঠি, আবার ভালোও অপরিসীম ও অনির্বচনীয়রূপে ভালো; জীবনের এমন-কোনো দিক নেই, মনের এমন-কোনো মহল নেই, দৃষ্টির এমন-কোনো ভঙ্গি নেই, যার সঙ্গে মহাভারত আমাদের পরিচয় করিয়ে না দেয়। শুধু পৃষ্ঠাসংখ্যায় নয়, জীবনদর্শনের ব্যাপ্তিতেও রামায়ণ অনেকটা ছোটো; কিন্তু কাব্য হিশেবে এবং কাহিনী হিশেবেও- তাতে ঐক্য বেশি, এবং আমরা যাকে কবিত্ব বলি তাতে রামায়ণ সম্ভবত সমৃদ্ধতর। এটা ভালোই, যদি আধুনিক সাহিত্যের ঐশ্বর্যজটিল বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে আমরা কখনো-কখনো বেরিয়ে পড়ি বাল্মীকির তপোবনে, পৃথিবীর কৈশোর-সারল্যে, মানবজাতির শৈশবের স্বতঃস্ফূর্ততায়।
দুই
ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু যাতায়াতের পথ বিঘ্নবহুল। সে-পথ সম্প্রতি সুগম ক’রে দিলো শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু-কৃত বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ। হাস্যরসিক আর ফলিত বিজ্ঞানীর, ভাষাবিজ্ঞানী আর ভাষাশিল্পীর যে সমন্বয় বসু-মহাশয়ে ঘটেছে, এই বিশেষীকরণের যুগে তা রীতিমতোই বিরল; এবং অধুনা তাঁর রঙ্গস্রোত প্রায়- রুদ্ধ ব’লে আমরা যতই না আক্ষেপ করি, সেই সঙ্গে এ-কথাও বলতে হয় যে তাঁর অবিশ্রাম সক্রিয়তাই আমাদের সৌভাগ্য। বিশেষত এই রকম সময়ে, যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রুশ ও মার্কিন লেখকদের বঙ্গানুবাদে বাঙালীর লেখনী এবং দুর্লভ কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র ভূরিপরিমাণে ক্ষয়িত হচ্ছে, তখনো যে বাল্মীকি অনুবাদ করবার মতো মানুষ দেশে পাওয়া গেলো, উপরন্তু সে-গ্রন্থের প্রকাশকও জুটলো, তাতে এমন আশা করবারও সাহস হয় যে বইখানা কেউ-কেউ প’ড়েও দেখবেন। অন্তত, বসু- মহাশয় সাধারণ পাঠকের পথে একটি কাঁটাও প’ড়ে থাকতে দেন নি; সংক্ষেপী- করণের নৈপুণ্যদ্বারা গ্রন্থের কলেবর সাধারণের পক্ষে সহনীয় করেছেন, অনুবাদ করেছেন গদ্যে, সহজ সরল বাংলায়, অপরিহার্য অল্প কিছু পাদটীকা মাত্র দিয়েছেন, ভূমিকা যেটুকু লিখেছেন তাতেও পাণ্ডিত্যের ভার চাপান নি। বস্তুত, বইখানা উপন্যাসের মতো আরামে প’ড়ে ওঠার কোনো বাধা যদি থাকে, সে শুধু মাঝে-মাঝে উদ্ধৃত বাল্মীকির মূল শ্লোকাবলি; আর সেগুলিও, বসু-মহাশয় ভূমিকায় ব’লেই দিয়েছেন (বোধহয় আমাদের শ্রমবিমুখতাকে ব্যঙ্গ ক’রেই), পাঠক ইচ্ছে করলে ‘অগ্রাহ্য করতে পারেন’। কিন্তু কোনো অর্থেই গ্রহণের অযোগ্য নয় সেগুলি; সংস্কৃতের সঙ্গে অল্পস্বল্প মুখচেনা যাঁদের আছে, এমন পাঠকেরও একটু খোঁচাতেই সন্ধি-সমাসের ফাঁকে-ফাঁকে রস ঝরবে, কেন না সৌভাগ্যক্রমে বাল্মীকির সংস্কৃত খুব সহজ। রাজশেখর বসুকে ধন্যবাদ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষা ও শরৎঋতুর মধুর বর্ণনাটুকু বাল্মীকির মুখেই তিনি আমাদের শুনিয়েছেন— এ-বর্ণনা কৃত্তিবাস বেমালুম বাদ দিয়েছেন ব’লে তাঁকে প্রশংসা করা যায় না, কেন না কবিত্ব, নাটকীয়তা এবং চরিত্রণ— তিন দিক থেকেই এই ঋতু-বিলাস সুসংগত ও সুন্দর। ঘনজটিল বনের মধ্যে চলতে-চলতে হঠাৎ যেন একটি স্বচ্ছনীল হ্রদের ধারে এলুম, সেখানে নৌকো আমাদের তুলে নিয়ে জলের গান শোনাতে লাগলো; ওপারে জটিলতর পথ, কুটিলতম কাঁটা— কিন্তু এই অবসরটুকু এমন মনোহরণ তো সেইজন্যই। বনবাসের
দুঃখ, সীতা-হারানোর দুঃখ, বালীবধের উত্তেজনা ও অবসাদ— সমস্ত শেষ হয়েছে, সামনে প’ড়ে আছে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা: দুই ব্যস্ততার মাঝখানে একটু শান্তি, সৌন্দর্য-সম্ভোগের বিশুদ্ধ একটু আনন্দ। এই বিরতির প্রয়োজন ছিলো সকলেরই— কাব্যের, কবির এবং পাঠকের, আর সবচেয়ে বেশি রামের। বর্ণনার শ্লোকগুলি রামের মুখে বসিয়ে বাল্মীকি সুতীক্ষ্ণ নাট্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বালস্বভাব লক্ষ্মণের সীতা-উদ্ধারের চিন্তা ছাড়া আর-কিছুতে মন নেই; শান্ত, শুদ্ধশীল রাম তাকে ডেকে এনে দেখাচ্ছেন বর্ষার বৈচিত্র্য, শরতের শ্রীলতা। বিরহী রামের সঙ্গে বিরহী যক্ষের তুলনা করলেই আমরা আদিকাব্যের সঙ্গে উত্তরকাব্যের চারিত্রিক প্রভেদ বুঝতে পারি: আদিকাব্যে সম্পূর্ণ সত্যের নিরঞ্জন প্রশান্তি, উত্তরকাব্যে খণ্ডিত সত্যের উজ্জ্বল বর্ণবিলাস। সীতার বিরহে রাম ক্লিষ্ট, কিন্তু অভিভূত নন; যদিও মুখে তিনি দু-চার বার আক্ষেপ করছেন, আসলে সীতার অভাব তাঁর প্রকৃতিসম্ভোগের অন্তরায় হ’লো না; আবার মেঘ দেখেই কালো চুল কিংবা চাঁদ দেখেই চাঁদমুখ স্মরণ ক’রে আকুল হলেন না তিনি। অথচ যক্ষের বিরহের চাইতে রামের বিরহ অনেক নিষ্ঠুর, রামের দুঃখ লক্ষ্মণের শতগুণ। সীতা কাছে নেই ব’লে প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপর অভিমান করলেন না রাম, তার গলা জড়িয়েও কাঁদলেন না: সৌন্দর্যে তাঁর নিষ্কাম, নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ, যেমন শিল্পীর। এর আগে এবং পরে নিসর্গ-বর্ণনার আরো অনেক সুযোগ ছিলো, কিন্তু বাল্মীকি সে-সমস্তই উপেক্ষা ক’রে গেছেন, কেন না এর আগে এবং পরে রাম নিরন্তর কর্মজালে জড়িত— এইখানেই, এই যুদ্ধযাত্রার পূর্বাহ্ণে রামের একটু সময় হ’লে। ভাবখানা এইরকম যেন নিরিবিলি ব’সে ঘাস, গাছ, আকাশ দেখতে তাঁর ভালোই লাগছে; যেন হৃদয়হীন যুদ্ধ আসন্ন জেনেই এই বিরল অবসরটুকুতে তিনি সীতার কথা ভাবছেন না, রাবণ বা সুগ্রীবের কথাও না— কিছু ভাবতে গেলেই যুদ্ধের কথা ভাবতে হয়, তাই কিছুই ভাবছেন না তিনি, মনকে শুধু ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেই সবুজ বনে,
যে-বনভূমি
ক্বচিৎ প্রগীতা ইব ষটপ্দৌঘে
ক্বচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠেঃ
ক্বচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈ :..’
তিন
আরো একটি কারণে কৃত্তিবাস যথেষ্ট নন, বাল্মীকির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের প্রয়োজন। সে-কারণ কী, এই গ্রন্থের ভূমিকাতেই তা বলা আছে, এবং বইখানা প’ড়ে আমরা শুধু সকৌতুকে নয়, সহর্ষেও জানি যে রাম-লক্ষ্মণেরা প্রচুর মাংস খেতেন, সব রকম মাংস খেতেন, গোসাপের মাংসও বাদ যেতো না— এমনকি অমাংসভোজনকে তাঁরা বলতেন উপবাস। সুরাতেও বিমুখ ছিলেন না তাঁরা— রাম নিজের হাতে সীতাকে মৈরেয় মদ্য পান করাচ্ছেন; আর হনুমান সীতার খবর নিয়ে লঙ্কা থেকে ফেরবার পর বানরদল যে-মাৎলামিটা করলে, রাম সেটার শাসন করলেন কিন্তু নিন্দা করলেন না। এই মধুবনের বৃত্তান্তটা— বোধহয় ভোক্তারা বানর ব’লেই কৃত্তিবাস গোপন করেন নি; কিন্তু রামান্বেষী ভরতের সৈন্যদলকে ভরদ্বাজ যে-রকম আপ্যায়ন করলেন, সেটা কৃত্তিবাসের সহ্য হ’লো না। পাশাপাশি দুটি অংশ তুলে দেখালেই আমার বক্তব্য বোঝা যাবে:
এমন সময় ব্রহ্মা ও কুবের কর্তৃক প্রেরিত বহু সহস্র স্ত্রী দিব্য আভরণে ভূষিত হয়ে উপস্থিত হ’ল। তারা যে পুরুষকে গ্রহণ করে তারা উন্মাদের তুল্য হয়। কাননের বৃক্ষসকল প্রমদার রূপ ধারণ ক’রে বলতে লাগল।
—সুরাপায়িগণ সুরা পান কর; বুভুক্ষিতগণ পায়স ও সুসংস্কৃত মাংস যা ইচ্ছা খাও। এক এক জন পুরুষকে সাত আট জন সুন্দরী স্ত্রী নদীতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গসংবাহন ক’রে মদ্যপান করাতে লাগল। পানভোজনে এবং অপ্সরাদের সহবাসে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ রক্তচন্দনে চর্চিত হ’য়ে বললে,
—আমরা অযোধ্যায় যাব না, দণ্ডকারণ্যেও যাব না, ভরতের মঙ্গল হ’ক, রাম সুখে থাকুন।
যারা একবার খেয়েছে, উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখে আবার তাদের খেতে ইচ্ছা হ’ল। সকলে বিস্মিত হয়ে আতিথ্যের উপকরণসম্ভার দেখতে লাগল— স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে অন্ন, ফলরসের সহিত পক্ক সুগন্ধ সূপ, উত্তম ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস, স্থালীতে পক্ক মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস, দধিদুগ্ধপূর্ণ অসংখ্য কলস, স্নান ও দন্ত- মার্জনের উপকরণ, দর্পণ, বস্ত্র, পাদুকা, শয্যা প্রভৃতি। ভরতের সৈন্যেরা মদ্যপানে মত্ত হ’য়ে নন্দনকাননে দেবগণের রাত্রি যাপন করলে। গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভৃতি নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল।
(রাজশেখর বসুর অনুবাদ)
ভোজনে বসিল সৈন্য অতি পরিপাটি।
স্বর্ণপীঠ স্বর্ণথাল স্বর্ণময় বাটি ॥
স্বর্ণের ডারব আর স্বর্ণময় ঝারি।
স্বর্ণময় ঘরেতে বসিল সারি সারি ॥
দেবকন্যা অন্ন দেয় সৈন্যগণ খায়।
কে পরিবেশন করে জানিতে না পায় ॥
নির্মল কোমল অঙ্গ যেন যূথিফুল।
খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হৈল ভুল ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস ॥
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ ।।
কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে।
আচমন করিয়া ঠাট কষ্টে উঠে খাটে ॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে সুললিত।
কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় কুহুগীত।।
মধুকর মধুকরী ঝংকারে কাননে।
অপ্সরা নৃত্য করে গীত আলাপনে।।
অনন্ত সামন্ত সৈন্য সেই গীত শুনি।
পরম আনন্দে বঞ্চে বসন্তরজনী ॥
সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই।
অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইনু হেতাই ৷
এ-সুখ এ-সংসারে কেহ নাহি করে।
যে যার সে যাউক আমি না যাইব ঘরে !!
(কৃত্তিবাস)
কত দূরে বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাস, দুয়ের আত্মায় ব্যবধান কী দুস্তর! অন্য সব প্রসঙ্গের মতো, ইন্দ্রিয়সুখের প্রসঙ্গেও বাল্মীকি একেবারে বৈকুণ্ঠ, তাই- যদিও ক্ষণিক, যদিও অলীক— বৈকুন্ঠকেই আমাদের চোখের সামনে এনেছেন তিনি, কাম- কল্পনার পরমতাকে; আর কৃত্তিবাসের মনে সংকোচ আছে ব’লে ভরদ্বাজের আশ্চর্য আতিথ্যে তিনি শুধু দেখেছেন ঔদরিকতার আকণ্ঠ উদারতা। বাল্মীকি ভরতসেনার মনে দেবত্বের বিভ্রম জন্মিয়েছেন, রাম-ভরত সম্বন্ধে তাদের উদাসীনতা যেন পদ্মভুকের আবেশ; আর কৃত্তিবাসের সৈন্যসামন্ত যেন প্রাকৃত জন, শাক-ভাত খেয়ে মানুষ, হঠাৎ বড়োদরের নেমন্তন্ন পেয়ে এত খেয়ে ফেলেছে যে আর নড়তে পারছে না। বাল্মীকির ভোজ্যতালিকা সুষম, সম্পূর্ণ এবং রাজকীয়; মদ্য-মাংস বাদ দিতে গিয়ে কৃত্তিবাস সুবৃহৎ ফলারের বেশি কিছু জোটাতে পারেন নি। জীবনের যেটা পার্থিব দিক, তাতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যে উদাসীন বা অনিপুণ ছিলো না, বাল্মীকিতে তার প্রমাণ প্রচুর— কিন্তু সেটা কিছু জরুরি কথা নয়, আর সে-কথা প্রমাণ করারই বা গরজ কিসের। শুধু এইটুকু বলে এ-প্রসঙ্গ শেষ করা যাক যে কৃত্তিবাস যে-
সভ্যতার প্রতিভূ তার অশন-বসন ‘রীতি-নীতি সবই অনেকটা নিচু স্তরের; আর বাল্মীকি, যদিও তপোবনবাসী ব’লে কথিত, তবু তিনি রাজধানীরই মুখপাত্র, শ্রেষ্ঠ অর্থে নাগরিক, তুলনায় কৃত্তিবাসকে মনে হয় রাজার দ্বারা বৃত হ’য়েও প্রাদেশিক, কেন না তাঁর রাজা নিজেই তা-ই। বিশ্বাসী বাল্মীকির পাপে কৃত্তিবাস বাঙালী মাত্র, শুধু বাঙালী; অর্থাৎ বাঙাল।
চার
রামায়ণের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা রাম-চরিত। যে-রামের নাম করলে ভূত ভাগে, সেই রাম নিষ্ঠুর অন্যায় করেছেন একাধিকবার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রামকে ‘অন্য সমালোচনার আদর্শে’ বিচার করাই চলবে না, ভেবে দেখতে হবে, যুগ-যুগ ধ’রে ভারতীয় মনে তাঁর কোন মূর্তিটি গ’ড়ে উঠেছে। রামচন্দ্রের এই প্রতিপত্তির মূল কোথায় তাও রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ ক’রে দেখিয়েছেন: রাম বালীবধ ক’রে সুগ্রীবকে রাজা করলেন, রাবণ-বধ ক’রে বিভীষণকে; কোনো রাজত্বই নিজে নিলেন না; মিতালি করলেন চণ্ডালের সঙ্গে, বানরের সঙ্গে, এই উপায়ে, অভ্রান্ত কূটনীতির দ্বারা, আর্য-অনার্যে সম্পূর্ণ মিলন ঘটিয়ে বিশাল ভারতের ঐক্যসাধন করলেন, ভারতীয় ইতিহাস সম্ভবত প্রথমত সেই ঐক্যসাধন। কালক্রমে তাঁর আদি কাহিনীর ‘মুখে-মুখে রূপান্তর ও ভাবান্তর’ হ’তে লাগলো; গণমানসে তিনি প্রতিভাত হলেন লোকোত্তর পুরুষরূপে, এমনকি অবতার-রূপে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অনুসরণ ক’রে বলা যায় যে আদি রামের মহিমা অনেকটা জুলিয়স সীজারের অনুরূপ; যে রাম-রাজ্য আর সাম্রাজ্য আসলে অভিন্ন; যে সাম্রাজ্যবাদের উচ্চতম আদর্শের মহত্তম ব্যঞ্জনা যেমন সীজার-জীবনে, তেমনি রাম-চরিতে। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞ, বাল্মীকি প’ড়ে তা ভালোই জানা যায়; শ্রেষ্ঠ এই কারণে যে কূটনীতির সঙ্গে ধর্মনীতিকে তিনি মোটের উপর মেলাতে পেরেছেন, যদিও মুমূর্ষু বালীর কানে তার নিধনের সমর্থনে যে-কথাগুলি তিনি জপলেন তাতে প্রকারান্তরে এই কথাই বলা হ’লো যে রাজনীতির ক্ষেত্রে নামলে অন্যায় থেকে অবতারেরও ত্রাণ নেই। …কিন্তু এইজন্যই কি রাম এত বড়ো? মস্ত বীর, মস্ত রাজা ব’লে? সাম্রাজ্যের অতুলনীয় স্থপতি ব’লে?
অনেকটা রবীন্দ্রনাথের কথাই মেনে নিয়ে বসু-মহাশয়ও ভূমিকায় বলেছেন যে আধুনিক যুগের সংস্কার নিয়ে রামায়ণ বিচার সম্ভব নয়। যেমন, তিনি যুক্তি দিয়েছেন, রাজ্যের খাতিরে ভার্যাত্যাগ আমাদের কাছে দুঃসহ, তেমনি রামচন্দ্রের আজীবন একপত্নীত্ব যে সেই হারেমবিলাসী যুগে কত বড়ো আদর্শের প্রতিরূপ, সেটাও আমাদের উপলব্ধির বর্হিভূত। … কিন্তু রামচন্দ্রকে কি আমরা বিচার করবো শুধু তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে? তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের চিরকালের আদর্শ যদি দেখতে না-পেলাম, তবে তিনি রাম কিসের। একটি বই স্ত্রী তাঁর ছিলো না, সেইজন্য কি তিনি বড়ো? না কি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ শত্রু ব’লে? শুধু এটুকুর জন্যই, কিংবা এই সমস্ত-কিছুর জন্যই, কি রামচন্দ্রের মহিমা ?
আধুনিক পাঠকের চোখে রাম রীতিমতো অ-রাম হ’য়ে ওঠেন তাঁর সীতা- বর্জনের সময়। অগ্নিপরীক্ষা তো সীতার নয়, রামের, আর সে-পরীক্ষার বিচারক আমরা। যুদ্ধ শেষ হ’লো; রাবণের মৃত্যু হ’লো; রাম বিভীষণকে বললেন, সীতাকে নিয়ে এসো আমার কাছে, সে স্নান ক’রে শুদ্ধ হ’য়ে আসুক। সীতা বললেন, স্নান? তাতে দেরি হবে— আমাকে এখনই নিয়ে চলো। কিন্তু স্নান তাঁকে করতে হ’লো, সাজতেও হ’লো, পালকি থেকে নামলেন রামের সভায়, বানর রাক্ষস ভল্লুকের ভিড়ে। কতকাল পরে দেখা! কত দুঃখের পরে! ‘লজ্জায় যেন নিজের দেহে লীন হ’য়ে’ স্বামীর মুখের উপর চোখ রাখলেন সীতা, আর তখন, তখনই, সেই রাক্ষস বানর ভল্লুকের ভিড়ে এত দুঃখে ফিরে-পাওয়া সীতাকে প্রথম দেখে কী-কথা বললেন রাম? বললেন:
আমি যুদ্ধে শত্রু জয় ক’রে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুষ দ্বারা যা করা যায় তা আমি করেছি। আমার ক্রোধ ও শত্রুকৃত অপমান দূর হয়েছে, প্রতিজ্ঞা পালিত হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি চপলমতি কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলে তা দৈবকৃত দোষ, আমি মানুষ হ’য়ে তা ক্ষালন করেছি। …তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম সুহৃদ্গণের বাহুবলে যা থেকে মুক্ত হয়েছি এ তোমার জন্য করা হয় নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যই এই কার্য করেছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে, নেত্ররোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ কষ্টকর। তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনর্গ্রহন করি তবে কি ক’রে নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দেব? যে উদ্দেশ্যে তোমাকে উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি মতি স্থির ক’রে বলছি… লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর কাছে যাও, অথবা তোমার যা অভিরুচি তা কর। সীতা, তুমি দিব্যরূপা-মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্যাবলম্বন করে নি।
( রাজশেখর বসুর অনুবাদ)
ছী-ছি— আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা কলরোল ক’রে ব’লে ওঠে— ছী-ছি! বিশেষ ক’রে ওই শেষের কথাটা— লক্ষ্মণ ভরত সুগ্রীব বিভীষণ যার কাছে ইচ্ছা যাও— কী ক’রে রামচন্দ্র মুখে আনতে পারলেন, ভাবতেই বা পেরেছিলেন কী ক’রে! এ তো শুধু হৃদয়হীন নয়, রুচিহীন; ‘নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেমন বলে’, এ তো তেমনি, সীতার এই উত্তর আমাদের সকলেরই মনের কথা। আর এখানেই শেষ নয়; অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর আবার সীতা-বিসর্জন; যদিও রামচন্দ্রের আন্তরাত্মা জানে যে সীতা শুদ্ধশীলা, তবু বাজে লোকেদের বাজে কথা কানে তুলে সীতাকে তিনি নির্বাসনে পাঠালেন— পাঠালেন ফাঁকি দিয়ে, যেন সীতার আশ্রমদর্শনের ইচ্ছা পূর্ণ করছেন, এই রকম ভান ক’রে। আবার বিরহ! কিন্তু রামের বিরহদুঃখের কোনো কথাই এবার আমরা শুনলুম না; রাজকার্যে নিবিষ্ট দেখলুম তাঁকে, যতদিন না অশ্বমেধ-যজ্ঞসভায় লবকুশকে দেখে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হ’লো। তাঁর আহ্বানে স্বয়ং বাল্মীকি এলেন সীতাকে নিয়ে সেই সভায়। সে-বার লঙ্কায় দর্শক ছিলো শুধু রাক্ষস বানর ভল্লুকের দল; এ-বার রাজসভায়, যজ্ঞভূমিতে, সকল গুরুজনেরা উপস্থিত, শ্রেষ্ঠ মুনিগণ উপবিষ্ট, রাক্ষস বানর এবং ‘বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কৌতূহলী হ’য়ে এল’, শেষপর্যন্ত স্বর্গের দেবতারাও না-এসে পারলেন না। ত্রিলোকের অধিবাসীর সামনে আবার সীতার পরীক্ষা— কিন্তু এ-পরীক্ষাও রামচন্দ্রের, আর বিচারক আমরা। সীতা মুখ নিচু ক’রে নিঃশব্দ, তাঁর হ’য়ে কথা বললেন বাল্মীকি। উত্তরে রাম বললেন:
…ধর্মজ্ঞ, আপনি যা বললেন সমস্তই বিশ্বাস করি।… লোকাপবাদ বড় প্রবল, তার ভয়েই এ’কে অপাপ জেনেও পুনর্বার ত্যাগ করেছিলাম আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। …জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাষা মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হ’ক।
রাম সীতাকে গ্রহণ করবেন, সে-জন্য অনুমতি চাচ্ছেন জগতের! এত দুঃখ সইতে পেরেছেন যে-সীতা, এ-দুঃখ তাঁর সইলো না,
…রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না— এই কথা যদি সত্য ব’লে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হ’য়ে আমাকে আশ্রয় দিন-
এই ব’লে তিনি পৃথিবীর বিবরে প্রবেশ করলেন।
সীতার দুঃখে পুরুষানুক্রমে আমরা কেঁদে আসছি। শ্রীযুক্ত বসুও তাঁর ভূমিকায় প্রশ্ন করেছেন: ‘দু-দুবার সীতাকে নিগৃহীত করবার কী দরকার ছিল?’ উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচনা নয়, এই পণ্ডিতপোষিত অনুমানে সান্ত্বনা, খুজেছেন তিনি’ কিন্তু উত্তরকাণ্ড না-থাকলে রামায়ণ এত বড়ো কাব্যই তো হ’তো না। লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা লক্ষ্মী মেয়ের মতো রামের কোলে ব’সে পুষ্পকে চ’ড়ে অযোধ্যায় এলেন, আর তারপর ঘরকন্না ক’রে বাকি জীবন সুখে কাটালেন— এই যদি রামায়ণের শেষ হ’তো, তাহ’লে কি সমগ্র ভারতীয় জীবনে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ’রে রামায়ণের প্রভাব এমন ব্যাপক, এমন গভীর হ’তে পারতো? বাল্মীকি যদি উত্তরকাও না-লিখে থাকেন, তবে সেইটুকু বাল্মীকিত্বে তিনি ন্যূন। উত্তরকাণ্ড যে-কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হোন, বাল্মীকিপ্রতিম নিশ্চয়ই; বস্তুত, রামায়ণকে অমর কাব্যে পরিণত করলেন তিনিই। যে-সীতার জন্য এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এমন সুদীর্ঘ ও সুতীব্র উদ্যম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হ’লো, ছাড়তে হ’লো স্বেচ্ছায়, এই কথাটাই তো রামায়ণের অন্তঃসার। যে-রাজ্য নিয়ে অত বড়ো কুরুক্ষেত্র ঘ’টে গেলো, সে-রাজ্য কি পাণ্ডবেরা ভোগ করেছিলেন? সব পেয়েও সব ছেড়ে গেলেন তাঁরা, বেরিয়ে পড়লেন মহাপ্রস্থানের মহানির্জনে। যুদ্ধে যখনই জয় হ’লো, রামও তখনই সীতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত।…’কর্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে নয়।’ …রামের যুদ্ধ, পাণ্ডবের যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলেছে তো এইজন্যই। তা না-হ’লে লোভীর সঙ্গে লোভীর যে-সব দ্বন্দ্ব মানুষের ইতিহাসে চিরকাল ধ’রে ঘ’টে আসছে, তার সঙ্গে এ-সবের প্রভেদ থাকতো না। লোভীর বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধরে, সে নিজেও লোভী ব’লে আধুনিক যুদ্ধে বীভৎসতা, শুধু হত্যার বীভৎসতা; কিন্তু পাণ্ডবের যুদ্ধে, রামের যুদ্ধে ফলে অধিকার নেই, অধিকার শুধু কর্মে আর তাই তার শেষ ফল চিত্তশুদ্ধি।
পাঁচ
রাম তাঁর কর্মকে মেনে নিয়েছেন। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কোন ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ তা তিনি জানেন, আর জীবনের প্রত্যেক অবস্থায়, সুখে এবং দুঃখে, সম্পদে এবং সংকটে সেই ভূমিকাটি সুসম্পন্ন করতে তিনি যথাসাধ্য সচেষ্ট। তাই তিনি অধৈর্যহীন, অক্লিষ্টকর্মা, শান্ত, শ্যামল, নিষ্কাম। বিপদে তিনি বিচলিত, কিন্তু বিহ্বল নন, সৌভাগ্যে তিনি প্রমত্ত নন, যদিও প্রীত। স্বর্ণমৃগ যখন মৃত্যুকালে স্বরূপ ধারণ করলে, তখন, রাক্ষসের মায়া বুঝতে পেরেও, রাম খুব বেশি ব্যস্ত হলেন না, ‘অন্য মৃগ বধ ক’রে মাংস নিয়ে’ তবে বাড়ি ফিরলেন। সীতা উদ্ধারের উদ্যোগ প্রারম্ভ হবার আগেই বর্ষা নামলো মাল্যবান পর্বতে, এই নিদারুণ সংকটে চার মাস চুপ ক’রে ব’সে থাকতে হবে ব’লে মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হলেন না. বরং এই অনভিপ্রেত নিষ্ক্রিয়তাকে বর্ষা-শরতের লীলাক্ষেত্র ক’রে তুললেন, আর শরতের শেষে যুদ্ধারম্ভের জন্য লক্ষ্মণকেই দেখা গেলো বেশি উদগ্রীব। রাম অধৈর্যহীন, বৈক্লব্যহীন, রাম ধীর স্নিগ্ধ গম্ভীর; যা করতে হবে সব করেন, কিন্তু এটা কখনো ভোলেন না যে এ-সমস্তই রঙ্গমঞ্চে তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকার অংশ মাত্র। বালীর মৃত্যুশয্যায় রাম নিজের সমর্থনের যে-চেষ্টা করলেন তা একেবারেই অনর্থক হতো, যদি- না তার মধ্যে এ-কথাটি থাকতো; ‘তোমাকে আমি ক্রোধবশে বধ করি নি, বধ ক’রে আমার মনস্তাপও হয় নি।’ এই অপার্থিবতা, এই ঐশ্বরিক উদাসীনতার মুখোমুখি আবার আমরা দাঁড়ালুম যুদ্ধকাণ্ডের শেষে, রাম যখন সীতাকে বললেন: ‘তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম… এ তোমার জন্য করা হয়নি।’ তোমার জন্য করিনি, তার মানে, আমার নিজের জন্য করিনি, শুধু করতে হবে ব’লেই করেছি। শুধু একবার, শেষবারের মতো সীতা যখন অন্তর্হিত হলেন, সেই একবার তিনি ‘মৈথিলীর জন্য উন্মত্ত’ হলেন, ‘জগৎ শূন্যময় দেখতে লাগলেন, কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না।’ তবু তো তার পরেও— যদিও, যেহেতু তিনি নররূপী বিষ্ণু, স্বর্গে সীতার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন তিনি ইচ্ছা করলে তখনই হ’তে পারতো— তার পরেও রাজস্ব করলেন ‘দশ সহস্র বৎসর’, সকল রকম ধর্মানুষ্ঠান করলেন, ভরত লক্ষ্মণের পুত্রদের রাজত্ব দিলেন, আর সর্বশেষে (এ-ঘটনাটা সর্বসাধারণে তেমনি সুবিদিত নয়) প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ত্যাগ করলেন প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য। ‘সৌমিত্রি, তোমাকে বিসর্জন দিলাম’, রামকে এ-কথাও নিজের মুখে বলতে হ’লো। প্রতিজ্ঞা- পালন তো উপলক্ষ মাত্র; আসল কথাটা এই যে, যেমন সীতাকে, তেমনি লক্ষ্মণকেও, স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে হবে— নয়তো মর্তের বন্ধন থেকে রাম মুক্ত হবেন কেমন ক’রে। স্বর্গারোহণের পথে যুধিষ্ঠিরকেও একে-একে ছাড়তে হ’লো নকুল সহদেব অর্জুন ভীম আর প্রিয়তমা পাঞ্চালীকে। স্বর্গের পথ নির্জন।
বাল্মীকিতে এ-কথাটা একটু জোর দিয়েই বার-বার বলা হয়েছে যে রাম অবতার হ’লেও মানুষ, নিতান্তই মানুষ। মনুষ্যত্বের মহত্তম আদর্শের প্রতিভূ তিনি, বিশেষ- কোনো একটি দেশের বা যুগের নয়, সর্বদেশের, সর্বকালের। দেহধারী মানুষ হ’য়ে, স্থানে ও কালে সীমিত হ’য়ে, যতটা মুক্ত, শুদ্ধ, সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র তা-ই। যদি তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণই হবেন, তবে মারীচের রাক্ষসী মায়ায় মজবেন কেন? কেন সীতাকে তাঁর মনে হবে ‘নেত্ররোগীর সম্মুখে দীপশিখা’র মতো? তাঁর এই উপমাতেই প্রমাণ করে যে তিনিও ছিলেন মনোবিকারের অধীন; সীতাকে দীপশিখার মতো বিশুদ্ধ জেনেও রাম যে তাঁকে সে-মুহূর্তে সহ্য করতে পারেন নি, তাতে রামেরই রুগ্ন অবস্থা ধরা পড়ে। মানুষ তিনি, নিতান্তই মানুষ, এবং সম্পূর্ণ মানুষ, তাই মানুষের দুঃখ তাঁকে সম্পূর্ণ জানতে হবে, এমনকি মানুষী অবমাননা থেকেও তাঁর নিস্তার নেই। তাই তো তাঁকে স্বীকার ক’রে নিতে হ’লো বালীহত্যার হীনতা, সীতাবর্জনের কলঙ্ক, শম্বুকবধের অপরাধ। যদি এ-সব না-ঘটতো, যদি তিনি জীবনে একটিও অন্যায় না-করতেন, তবে তাঁর নরজন্ম সার্থক হ’তো না, মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকতো, তবে তিনি হতেন নিয়তির অতীত, প্রকৃতির অতীত, অর্থাৎ আমরা তাঁকে আমাদের একাত্ম ব’লে অনুভব করতে পারতাম না— আর তাহ’লে রামায়ণের কাব্যগৌরব কতটুকু থাকতো? রাম করুণাময়, পতিতপাবন, তিনি পা ছোঁওয়ালে অহল্যা বাঁচে, রাবণ সুদ্ধ তাঁর হাতে মরতে পেয়ে ধন্য; তবু তো কারোরই— কোনো অন্ধ ভক্তেরও— তাঁকে বুদ্ধ বা যীশুর মতো মনে হয় না। আদিকবির নির্ভুল বাস্তবতা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে তিনি মহামানব নন, কিন্তু তিনি যে মানব, এই সত্যটাই মহান।
রামায়ণের ঘটনাচক্র এই মনুষ্যত্বের বহুলবিচিত্র ব্যঞ্জনার উপলক্ষ মাত্র। ‘মাইকেল’ প্রবন্ধে আমি প্রশ্ন উত্থাপন করেছি; রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন কেন? শ্রীযুক্ত বসুর বইখানাতে এ-প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করলাম; যে-উত্তর আমার মন চেয়েছিলো, তা সে পেলো না। আমার মনে হয় যে রামের দিক থেকে সমস্তটাই ছল; সমস্তটাই লীলা। রাম প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত পাঠ মুখস্থ ক’রেই রঙ্গমঞ্চে নেমেছেন, কিসের পর কী তা তিনি সবই জানেন, তবু যেন জানেন না; মহৎ অভিনেতার মতো আমাদের মনে এই মোহ জন্মাচ্ছেন যে ঘটনাবলি তাঁর পক্ষে অপ্রত্যাশিত, নিয়তি তাঁর কাছেও স্বৈরিণী, যেন এটা অভিনয় নয়, জীবন। জটায়ুকে পরাস্ত ক’রে রাবণ যখন সীতাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন ‘দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রাবণবধের সূচনায় তুষ্ট হলেন’; সীতাহরণটা আর-কিছু নয়, শুধু রাবণবধের ছল। আর রাবণ- বধও আর-কিছু নয়, শুধু রামের কর্ম-উদযাপনের উপলক্ষ। সীতা-উদ্ধারের জন্য এত পরিশ্রমই বা কেন, ইচ্ছে করলে রাম কী না পারেন। কিন্তু ঐ ইচ্ছে করাটা তাঁর ভূমিকায় নেই, কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করেন না তিনি, তাঁকে মেনে নিতে হয় বর্ষার বাধা, সমুদ্রের ব্যবধান, ঘটনার দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিকূলতা; বালীকে মেরে সুগ্রীবকে রাজত্ব দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় বানর-সেনা, যে-বানর মানুষেরও অধম; দীন, দুর্বল, বর্বর সৈন্যদল নিয়ে এগোতে হয় চতুর, সুসংবদ্ধ, যন্ত্রনিপুণ দানবের বিরুদ্ধে। কেন? না, এটাই মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতার উপায়। হনুমান অনায়াসেই সীতাকে পিঠে ক’রে নিয়ে আসতে পারতেন, তা তিনি চেয়েওছিলেন, যুদ্ধের তাহ’লে প্রয়োজনই হ’তো না; কিন্তু সে তো হ’তে পারে না, তাতে রামের পূর্ণতার হানি হয়। সীতা-উদ্ধার হ’লেই তো হলো না, সেটা ত্যাগের ও দুঃখের দীর্ঘতম পথে হওয়া চাই; কেন না সীতা-উদ্ধার তো উপলক্ষ, লক্ষ্য হ’লো রামের সর্বাঙ্গীণ মরত্ব-ভোগ। তাই হনুমানের প্রস্তাবে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন না সীতা, তা প্রত্যাখ্যান ক’রে বললেন:
…সমস্ত রাক্ষসদের বধ ক’রে যদি তুমি জয়ী হও, তাতে রামের যশোহানি হবে। রামের সঙ্গে তুমি এখানে এস, তাতেই মহৎ ফল হবে। যদি রাম এখানে এসে দশানন ও অন্য রাক্ষসদের বধ ক’রে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান তবেই তাঁর যোগ্য কাজ হবে। তুমি একাই কার্য সাধন করতে পার তা জানি, কিন্তু রাম যদি সসৈন্যে এসে রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ক’রে আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁর উচিত কার্য করা হবে।
রামায়ণের চরিত্র সাধারণত পুনরুক্তি করে না, কিন্তু সীতা হনুমানকে এই কথাটি দু-বার বলছেন। তাঁর এ-আগ্রহ কি উদ্ধারের জন্য? তা যদি হ’তো তবে তো তিনি তৎক্ষণাৎ হনুমানের পৃষ্ঠে আরূঢ় হতেন। না, আগ্রহ এইজন্য যাতে রামচন্দ্রের পূর্ণতা অবরুদ্ধ না হয়; আর সে-আগ্রহ শুধু সীতার নয়, কাব্যের স্রষ্টার, কাব্যের ভোক্তার।
ছয়
রামায়ণে অসংগতি অসংখ্য। অনেক ক্ষেত্রেই কবি আমাদের সম্ভাব্য কৌতূহলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক’রে গেছেন। উপেক্ষিতা উর্মিলাকে বিখ্যাত করেছেন রবীন্দ্রনাথ; শ্রীযুক্ত বসুও ভূমিকায় কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আদি-কবির অবহেলার তালিকা ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছও নয়। উদাহরণত, বালীপত্নী তারাকে তিনি এমন ক’রে এঁকেছেন যেটা রীতিমতো মর্মঘাতী। পতির মৃত্যুতে চীৎকার ক’রে কাঁদতে শুনলুম তাঁকে, আর তার পরেই দেখা গেলো ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সামনে তিনি বেরিয়ে এলেন সেই অন্তঃপুর থেকে, যেখানে ‘সুগ্রীব প্রমদাগণে বেষ্টিত হ’য়ে রুমাকে আলিঙ্গন ক’রে স্বর্ণাসনে ব’সে আছেন’, ‘মদবিহ্বলা’ তিনি, স্খলিতগমনা, এসে লক্ষ্মণের কাছে তৈলাক্ত ওকালতি করলেন সেই সুগ্রীবকে নিয়ে, যে-সুগ্রীব যথার্থ বালীহন্তা। আমাদের অবাক লাগে বইকি।… কিন্তু আদিকবি উদাসীন, আধুনিক কালের সচেতন শিল্পী তিনি নন; শিশুর শিল্পহীনতার পরম শিল্পে তিনি অধিকার করেন আমাদের, কত বাদ দিয়ে যান, কত ভুলে যান, কত এলোমেলো অতিরঞ্জন, অবান্তরতা; কোনো কৌশল জানেন না তিনি, সাজাতে শেখেন নি; আমাদের ধ’রে রাখে শুধু তাঁর সত্যদৃষ্টি, তাঁর মৌল, সহজ, সামগ্রিক সত্যদৃষ্টি। তাঁর বাস্তবতা এতই বিরাট ও সর্বংসহ যে একদিকে যেমন ঘটনাবর্ণনে কি চরিত্রচিত্রণে নিছক বাস্তবসদৃশতার জন্য তিনি ব্যস্ত নন, তেমনি ডিকেন্স বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রত্যেকটি পাত্রপাত্রীর শেষপর্যন্ত কী হ’লো, তা জানাবার দায় থেকেও তিনি মুক্ত। যে-রকম একটি সুযোগ পেলে আমরা আধুনিক লেখকরা ব’র্তে যাই, সে-রকম কত সুযোগ তিনি হেলায় হারিয়েছেন— সেগুলি কোনোরকম সুযোগ ব’লেই মনে হয় নি তাঁর। শুধু যে উর্মিলাকে একেবারে ভুলে গিয়েছেন তা নয়, লক্ষ্মণকেও ভুলেছেন, কেন না একবার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো না লক্ষ্মণের, বনবাসযাত্রার সময় স্ত্রীর কাছে একটু বিদায় পর্যন্ত নিলেন না। আর কৈকেয়ীকেও বলতে গেলে সেই একবারই আমরা দেখলুম; কিন্তু পরে কি তাঁর অনুশোচনা হয় নি? আমাদের এ-সব জিজ্ঞাসার উত্তর রামায়ণে নেই, আছে আমাদের হৃদয়ে। আর সেই হৃদয়লিপির রচয়িতাও রামায়ণের কবি। আমরা যে উর্মিলার কথা ভাবি, লক্ষ্মণের হ’য়ে আমাদের যে মন-কেমন করে, কৈকেয়ীর হ’য়ে আমরা যে অনুশোচনা করি— এ-সমস্তই কি বাল্মীকিরই ব’লে দেয়া নয়? আদি কবির শিল্পহীনতার চরম রহস্য এইখানে যে আমরা তাঁর পাঠক শুধু নাই, তাঁর সহকর্মী, তিনি নিজে যা বলতে ভোলেন, সে-কথা রচনা করিয়ে নেন আমাদের দিয়ে। কেউ হয়তো বলবেন যে রাম ছাড়া অন্য সকলেই তাঁর কাছে উপেক্ষিত; অন্য সব চরিত্রই খণ্ডিত, মাত্র একটি লক্ষণসম্পন্ন; লক্ষ্মণ শুধুই ভাই, হনুমান শুধুই সেবক, রাবণ শুধুই শক্তিশালী— রাম ও সীতা কেউ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয়। কিন্তু রামের সম্বন্ধেই কবির উপেক্ষা কি কম! রাম প্রেমিক, রাম-সীতার জীবন দাম্পত্যের মহৎ আদর্শ, কিন্তু তাঁদের যুগল-জীবনের পরিধি কতটুকু! বলতে গেলে সারা জীবনই তো রামকে সীতাবিরহে কাটাতে হ’লো। এ-বিরহে সীতার প্রতি কবির করুণা প্রচুর, কিন্তু রাম সম্বন্ধে তাঁর মুখে বেশি কথা নেই। যখন সীতাহরণ, যখন পুনর্জিতার প্রত্যাখ্যান, যখন গণরঞ্জনী দ্বিতীয় সীতাবর্জন—এই তিনবারের একবারও রামকে তেমন শোকার্ত আমরা দেখলাম না; মনে-মনে বললাম, রাজধর্মের তাগিদে না-হয় বাধ্যই হয়েছিলেন, তাই ব’লে দুঃখও কি পেতে নেই! …কিন্তু রামের উদাসীনতায়, কিংবা রামের প্রতি কবির উদাসীনতায়, আমাদের মনে যে-দুঃখ, সেই দুঃখই তো রামের যে-রাম সীতার জন্য কাঁদছেন, সে-রাম তো আমরাই। নাটক রঙ্গমঞ্চে আরম্ভ হ’য়ে শেষ হ’লো প্রেক্ষাগৃহে, কিংবা রঙ্গমঞ্চে শেষ হবার পর প্রেক্ষাগৃহে চলতে লাগলো; রঙ্গমঞ্চে একজন রাম যা করলেন, তার জন্য প্রেক্ষাগৃহের লক্ষ-লক্ষ রামের কান্না আর ফুরোয় না। হয়তো উদাসীনতাই অভিনিবেশের চরম; হয়তো উপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষা; হয়তো শিল্পহীনতার অচেতনেই শিল্পশক্তির এমন একটি অব্যর্থ সন্ধান হিলো, যা ফিরে পেতে হ’লে মানব-জাতিকে আবার নতুন ক’রে প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে।
অলংকরণ- রাতুল চন্দরায়